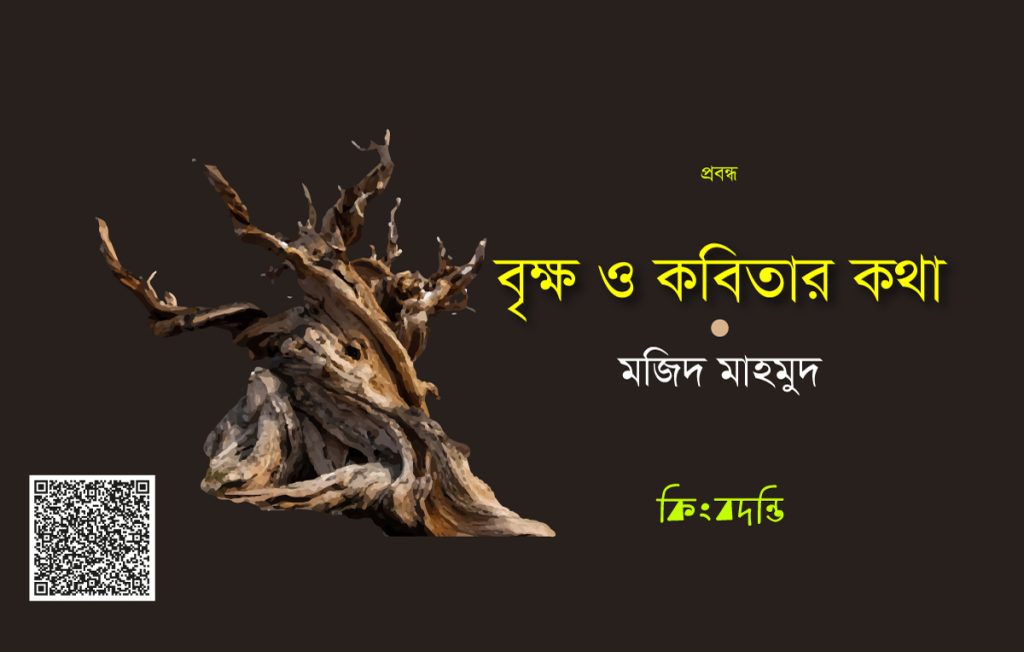মাতৃগর্ভে বসবাস করে যেমন মায়ের রূপ-দর্শন অসম্ভব তেমন পৃথিবী তথা বিশ্বব্রহ্মান্ডের স্তন্যে লালিত মানুষ শত সহস্র বছরের চেষ্টায় খুব কমই তাকে দেখতে পায়। মায়ের প্লাসেন্টার মধ্যে যখন সে ভাসতে থাকে পা ও মাথা কোনো পাটাতনের উপর না রেখেই সে দিব্বি প্রাণজ জীবন অতিবাহিত করে। আবার যখন সে মাতৃগর্ভের বাইরে আসে তখন আপনার রূপ থেকে সে মাকে আলাদা করতে পারে না- মা নিজেও তখন স্বতন্ত্র প্রাণের অংশ হয়ে পড়ে। বৃহত্তর অর্থে পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরে যে শূন্যতার সংসার সাজানো রয়েছে যেখানে লক্ষ কোটি ছায়াপথ, গ্ল্যাক্সি ও বৃহদকার ব্ল্যাকহোল আমাদের জানা ও অজানা পথে অপেক্ষা করে আছে তার সকল কিছু মিলেই আমাদের প্রকৃতি, আমাদের নিসর্গ তথা এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সংসার।
আমরা কেউ জানি না-না জ্ঞানি না বিজ্ঞানি সবাই কিছুটা অনুমান করে বলে কিভাবে এই বিশ্ব প্রকৃতির জন্ম হয়েছিল। বিশ্বপ্রকৃতির জন্মের উপর কানো স্থির তত্ত্ব নেই- আছে হাজারো হাইপোথিসিস, আছে ধর্মীয় মেটাফর। এমনকি কোনো এক বিজ্ঞানি বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টির যে তত্ত্ব ইতোপূর্বে দিয়েছিলেন কালক্রমে তারও পরিবর্তন হয়ে গেল বিগব্যাঙ্ক থিউরির প্রবর্তক স্টেফেন হকিংস হতে পারে তার সর্বশেষ উদাহরণ। আবার এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মীয় মেটাফরগুলো এক মাত্রায় ক্রিয়াশীল নয়। এখানেও মানুষ ভেবেছেন এতবড় বিশ্বপ্রকৃতির পিছনে কোনো কার্যকরণ নেই সর্বশেষ উপসংহার নেই ক্ষুদ্র মানুষ তা বিশ্বাস করতে পারে না।
আর এই বিশাল প্রকৃতির মধ্যে মানুষ নিজেকে একমাত্র চিন্তাশীল ও শ্রেষ্ঠপ্রাণী বলে ধার্য করে আসছে। অতএব, তার সকল কিছুতে রয়েছে চিন্তা ও নিজেকে রক্ষা করবার অধিকার। কিন্তু প্রেক্ষাপট থেকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখবো, পৃথিবীতেই এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যাদের পরিবৃত্তি ঠিক মানুষের মতো। তারাও মানুষের মতো ঘর বাঁধে, তাদের রয়েছে রাজা-রানি, দাস-দাসী ও সন্তানকে লালান-পালন ও শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া। একই প্রজন্মের মধ্যে তারা লড়াই করে বেঁচে থাকে। শত্রুর উপরে চালায় প্রবল আক্রমণ বন্দিদের দাসে পরিণত করে।
১.
মানুষ পৃথিবী মায়ের এক ক্ষুদ্র সন্তান প্রায় সে ভুলে থাকে তার আলাদা জীবন আছে; কখনো ভেবে থাকে এ এক জড় পদার্থ; কিন্তু জড় পদার্থ কিভাবে জীবন দান করতে পারে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করে থাকেন প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে এই পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। আগে সূর্যের গর্ভে ছিল তার আদরে বসবাস। মায়ের প্লাসেন্টার ভেতর যেমন সন্তান বেড়ে ওঠে পৃথিবীও ঠিক সূর্যের গর্ভে পরম আদরে বেড়ে উঠেছিল; যদিও আমরা বলতেও পারব না কে তার বাবা; নানা ঠাকুর্দাও ছিল নিশ্চয়। সুখে-দুখে দহনে পৃথিবী প্রথম ঘাতসহ হয়েছিল সূর্যের সান্নিধ্যে; তারও ছিল আগুনের শরীর ভরপুর ছিল তার শরীর গ্যাসীয় পদার্থে।
সময় ধারণ করে আছে আমাদের পৃথিবীর জীবন। পৃথিবীও এর ব্যতিক্রম নয়। ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকলো তার রোষ, শরীর থেকে ঝরে পড়তে থাকলো তার সূর্যের রেশ।
কেউ আজ আমরা ভাবতে পারি না তার ভয়াবহ উত্তাপ। কিন্তু আমরা বলতে পারব না যে সব কিছু এমনিতেই সংঘটিত হয়েছিল; সূর্য কিংবা পৃথিবীর নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল কিনা তাও আমরা জানি না। সূর্যের মনের গভীরে হয়তো জন্ম নিয়েছিল এক মহানন্দ এক মহাপরিকল্পনা। ভেবেছিলেন আগুনের শরীর থেকে তিনি জন্ম দেবেন পানির সন্তান। তাই তিনি তার কন্যাকে এক মহা উৎক্ষেপনে নিক্ষিপ্ত করলেন মহাশূন্যতায়। বিচ্ছিদের বেদনায় কান্নার গহনে কেটে গেল তার শত সহস্রকোটি বছর। সময় সকল দুঃখের প্রলেপদায়িনী। সময় ধারণ করে আছে আমাদের পৃথিবীর জীবন। পৃথিবীও এর ব্যতিক্রম নয়। ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকলো তার রোষ, শরীর থেকে ঝরে পড়তে থাকলো তার সূর্যের রেশ। গ্যাসীয় পদার্থগুলো ক্রমান্বয়ে জমাট বাঁধতে থাকলো; জন্ম হলো বরফ ও পানির সমুদ্র। পানি থেকে জেগে উঠলো জীবন। এ কথা নিঃসন্দেহ করে বলা যায় পৃথিবীর প্রাণউদ্ভিদ জগতে মানুষ হলো নবীন অতিথি। কিন্তু বৃক্ষবিহীন মানুষের পৃথিবী কল্পনা করা যায় না। মানুষের পূর্ব-পুরুষ ছিল বৃক্ষ। বৃক্ষকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন পল্লবিত হয়েছে।
২.
বৃক্ষ জীবনের অক্ষবিন্দু। উদ্ভিদকে কেন্দ্র করেই মানুষের জীবন আবর্তিত। মানুষ পৃথিবীতে আসার আগেই উদ্ভিদ এই ধরণীকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছিল। মায়ের মতো উদ্ভিদ বসুধার বুকে জমা করেছিল স্তন্য। মানুষ উদ্ভিদের স্তন্যে লালিত। মানুষকে তাই উদ্ভিদপায়ী প্রাণী বলা যায়। পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেই উদ্ভিদ মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বাতাস তৈরি করেছিল। প্রতিটি পল্লবকে আজান তৈরির কারখানায় রূপান্তর করেছিল। মানুষের নিঃশ্বাসে নিঃসৃত কার্বনকে শুষে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিল। মৃত্তিকা উদ্ভিদ মানুষ (প্রাণী), এই ত্রিভুজ বৃত্তের মধ্যেই রক্ষিত হয়েছে পৃথিবী নামক গ্রহের স্বাতন্ত্র্য জীবন। উদ্ভিদ ছাড়া পৃথিবীতে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। উদ্ভিদকে সংহার করেই আমরা জীবন ধারণ করি। একার্থে উদ্ভিদই আমাদের জীবন দান করে।
নন্দন উদ্যানের বৃক্ষই মানুষকে প্রথমে পৃথিবীর জীবনের পথে আহ্বান করেছিল। তাকে জ্ঞান দান করেছিল। দিয়েছিল সৃষ্টি এবং প্রজন্মের ধারণা। তাই গন্দম ভক্ষণের অপরাধে তাকে স্বর্গ ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু বৃক্ষ মানুষকে ত্যাগ করেনি। এই গ্রহে প্রাণিজগতে হয়তো বহু বিবর্তন ঘটেছে কিন্তু বৃক্ষহীন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব কখনও ছিল বলে মনে হয় না। মানুষ পৃথিবীতে আসার আগে বৃক্ষ এসেছিল সত্য; কিন্তু পৃথিবীতে বৃক্ষযুগ আসতেও সময় লেগেছিল শত সহস্র কোটি বছর।
পৃথিবীতে মানুষের অভিযাত্রার সবচেয়ে বড় পর্যায় শিকার যুগ থেকে কৃষিযুগে প্রবেশ করা। কৃষিযুগ মানে বৃক্ষযুগ। অনন্ত সম্ভাবনার যে যুগের কখনও অবসান হবে না। মানুষ ব্যাধের পোশাক ছেড়ে যখন থেকে কৃষকের পোশাক পড়েছে তখন থেকেই মানুষ মূলত অস্তিত্বের শঙ্কা মুক্ত হয়েছে। উদ্ভিদ আমাদের এভাবে পরিবেষ্টন করে আছে যে আমরা কখনও এর আলাদা অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি না।
বৃক্ষ জীবনের এক অমিত সম্ভাবনার নাম। প্রাণীর ত্বকের নিচে মূলত একটিই প্রাণী। তাকে হত্যা করলে ওখানেই তার চূড়ান্ত অবসান। কিন্তু একটি গাছ কাটার পরে তার শিকড় থেকেও আরেকটি গাছ জন্ম লাভ করে।
বৃক্ষ জীবনের এক অমিত সম্ভাবনার নাম। প্রাণীর ত্বকের নিচে মূলত একটিই প্রাণী। তাকে হত্যা করলে ওখানেই তার চূড়ান্ত অবসান। কিন্তু একটি গাছ কাটার পরে তার শিকড় থেকেও আরেকটি গাছ জন্ম লাভ করে। মানুষ যখন কৃষি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে তখন থেকে তার মরণের বোধও কমে গেছে। মানুষ তখন থেকে বোধ করতে শুরু করেছে, মানুষ ঠিক কোন একক মানুষ নয়, মানুষ জীবন বৃক্ষের এক একটি শাখা, মরণের মধ্যে দিয়ে যার সম্পূর্ণ অবসান হয় না। যিশু যখন বলেন, ‘আমি আঙুর কুঞ্জ, তোমরা তার লতা’ তখন আমরা বুঝতে পারি জীবনের পারস্পারিক সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কৃষি সংস্কৃতি মানুষকে স্মরণ করে দিয়েছে, মানুষও মাটির উদর থেকে উৎপন্ন। পৃথিবী আমাদের মা আমরা এই ধরিত্রী মাতার সন্তান। এই মাটির নির্যাস থেকে যেমন আমরা উৎপন্ন, তেমনি প্রতিটি প্রাণী, বৃক্ষরাজি এমনকি একটি ক্ষুদ্র ঘাসকেও গভীর মমতায় জন্মদান করেছে এই বসুমাতা। একই মায়ের সন্তানদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন লিঙ্গ এবং বর্ণের পার্থক্য থাকে তেমনি ধরণী মাতার সন্তানদের মধ্যেও কেউ মানুষ কেউ প্রাণী আবার কেউ বৃক্ষ কিংবা উদ্ভিদ নামে পরিচিত। সুতরাং এই উদ্ভিদকুল আমাদের ভাই আমাদের বোন। তাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন এক গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ।
সচেতন হৃদয়বান মানুষের কাছে বৃক্ষ এক অপার বিস্ময়, অসীম গুরুত্বের অধিকারী। বৃক্ষ মানুষের কাছে অনেক ক্ষেত্রে আবেগী অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে। মানুষ বৃক্ষ হওয়ার সাধনা করেছে। বৃক্ষের মতো অভিযোগহীন জীবন, যে জীবনের লক্ষ্য ছাড়িয়ে যাওয়া, অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করা। গাছের সাধনা ছিল সিদ্ধার্থের। বোধিদ্রুম এখনও তাঁর বাণী বহন করে চলেছে। প্রাচীন সাহিত্যে বিশেষ করে ভারতবর্ষের সাহিত্যে, ধর্ম ও জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে অরণ্য এবং বৃক্ষের এক আলাদা অবস্থান ছিল। বৃক্ষ ও অরণ্যকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জীবনের ধর্ম ও সংস্কৃতি। বৃক্ষ নেই তো ভারতীয় তপোবন নেই। তপোবন নেই তো বিদ্যা ও ধর্ম নেই। ভারতীয় জীবনের এক প্রধান সাধনা ছিল অরণ্যের কাছে ফিরে যাওয়া। তৈরি হয়েছে বানপ্রস্থের বিধান। প্রাচীন সাহিত্যেও বৃক্ষের এক আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে।
উদ্ভিদ ও মানুষ পাশাপাশি জড়াজড়ি করে বাস করেছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলমে আমরা এই প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই। উদ্ভিদ আর কণ্বমুনির আশ্রমের বাসিন্দাদের আলাদা করে চেনা যায় না। শকুন্তলা ও তার প্রিয়ংবদা অনসূয়া সখিদ্বয় বৃক্ষের মমতায় লালিত হয়েছে। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করছেন তখন কণ্বমুনি, ‘তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের জলসেচ না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি, ভূষণ প্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল¬বভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।’… ‘শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না! এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণী! শাখাবাহু দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন করো; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! । আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পন করিলাম।’ (শকুন্তলা: বিদ্যাসাগর)
বৃক্ষ ও অরণ্যের সঙ্গে আদি মানুষের প্রাণের মিলন ঘটেছিল প্রাচীন সাহিত্যের প্রায় সর্বত্র তার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। সীতার বনবাস কিংবা রামায়ণ মহাভারত, অরণ্যের প্রাণের মধ্যে এসবের অবস্থান। প্রাচীন সাধক এবং কবিরা নাগরিক ছিলেন না। অরণ্যের আত্মার মধ্যে ছিল তাদের বসবাস। বৈষ্ণব সাহিত্যে কদম্ব ও তমাল বৃক্ষের মাহাত্ম্য লক্ষ্য করা যায়। কদম্ব ও তমাল ছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্য অচল, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তমাল কৃষ্ণের রং ধারণ করে তমাল কৃষ্ণের তুল্যমূল্য লাভ করেছে। অনেক বৃক্ষের সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতিও জড়িয়ে আছে বিশেষকরে ভারতবর্ষে। ইসলামের নবীও বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষের যত্নের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও ভারতবর্ষের মতো মরুভূমিতে গাছ ছিল না তবু গাছের প্রতি ছিল তাঁর অসম্ভব মায়া। তিনি গাছ লাগানকে বলেছেন অবিনশ্বর পুণ্য কর্ম। মানুষ মরে গেলেও যার সুফল ভোগ করবে। একটি গাছ লাগানর কারণেও একজন মানুষ তার কৃত অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি শত্রুতা করে কোন বৃক্ষ নিধন করল তবে সে ধ্বংস হয়ে গেল। এই পাপ কোন পয়গম্বরকে হত্যার চেয়েও বেশি। কোন মুসলমান মারা গেলে তার কবরের উপরে সজীব কোন বৃক্ষ পুঁতে দেয়া হয়। জীবন্ত বৃক্ষ মৃত মানুষের জন্য দোয়া করতে থাকে। এই যে ধারণা, যার গুরুত্ব অপরিসীম।
আধুনিক কবি কিংবা নাগরিক কবিরা বৃক্ষকে ভুলে যাননি। ভোলা সম্ভব নয় কখনও। বৃক্ষ ও অরণ্যের এই দুঃসময়ে মনে পড়াটি কেবল সুখের নয় বেদনারও। রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষ নিয়ে অরণ্য-প্রকৃতি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছিলেন ‘বনবাণী’ (১৯২৬)। নিসর্গ জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল গভীর। সে সম্পর্কের মধ্যে কোন কাব্যিক চাতুর্য ছিল না। তাঁর রচনা পাঠ করলে মনে হয় তিনি যেন প্রকৃতির সন্তান। তাঁর ‘বনবাণী’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা অংশটি পাঠকের জন্য উদ্ধার করার লোভ সামলাতে পারছি না।
“আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছায় প্রাণের প্রথমত স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া উঠে সেও ওই গাছের ভাষায়, কথার কোন স্পষ্ট মনে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।
ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কূলে যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে ‘শান্তম শিবম অদ্বৈতম’। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। ‘এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি’ দেখি ফুলে ফলে পল¬বে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।
বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলন সঙ্গীতে বদ-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত¡ পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন- দুই-এ মিশে আছে। শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, ‘বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ’- প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই পৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গি, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালীনি সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।
এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কতদিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-পৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়- তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ- অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সঙ্গীতে। এই আমার অন্তর্গুঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরমসুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।”
রবীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থে কবিতার সংখ্যা ছিল মোট ২০টি এবং সবগুলো কবিতাই ছিল বৃক্ষ বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাববিলাসী বৃক্ষপ্রেমী কবির মতো কবিতা রচনা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বৃক্ষের বংশ বিস্তারের জন্যও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বৃক্ষ রোপণ করেছেন। বৃক্ষ রোপণ উৎসবকে কেন্দ্র করে গান রচনা করেছেন। এবং প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের তপোবনের আদলে শান্তি নিকেতনের পরিকল্পনা করেছেন। এর লক্ষ ছিল আজীবন বৃক্ষের সঙ্গে থাকা। রবীন্দ্রনাথেরও সখ ছিল কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণের। কালিদাসের প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক অদ্ভুত ঐক্যও ঘটেছিল। বনবাণী ছাড়াও রবীন্দ্র রচনাবলীর পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অরণ্য-প্রকৃতির হিরন্ময় কুচি। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের বাংলা কবিতার প্রধান অনুষঙ্গ ছিল, বৃক্ষ প্রকৃতি। কবির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটা কেমন যেন অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। কবি বললে এখনও অনেকেই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিষয়গুলো নিয়ে কবি কাব্য রচনা করবেন। যদিও পরবর্তী সময়ে কবি এবং কবিতার ধারণা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, কবিতায় কেবল সৌন্দর্য নয় কুৎসিত বিষয়গুলোও যে সমন্বিত হতে পারে তার নিদর্শন ঘটেছে।
কাজী নজরুল ইসলামের সারা জীবনই গিয়েছে বিপ্ল¬বের গান গাইতে। তবু তাঁর রোম্যান্টিক কাব্য-মানস ছিল প্রেম প্রকৃতির পক্ষে তাঁর গান কবিতায় তার উদাহরণ আছে প্রচুর। তিনি ‘বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি’ নামে একটি অনিন্দ্য সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। কবি-প্রেয়সী এবং কবি জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা হয়ে উঠেছে গুবাক বৃক্ষের সুখ-দুঃখ। নজরুল ইসলাম গুবাক বৃক্ষে মানবত্ব আরোপ করেছেন। তার বৃক্ষ অনুভূতিশীল বৃক্ষ। কবি বৃক্ষের মুখের বাণী শুনতে না পারলেও হৃদয়ের বাণী শুনতে পান।
তিরিশের দশকে বাংলা কবিতার যে আন্দোলন হয়েছিল তার সঙ্গে আধুনিক নাগরিক মনের সংঘাতটি বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেখান থেকেও বৃক্ষ কিংবা প্রকৃতি কবিদের হৃদয় থেকে তিরোহিত হয়নি। বরং অন্য মাত্রায় তা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বৃক্ষকে ধ্বংস করেই নগর গড়ে উঠেছে। তিরিশের প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশ তো প্রকৃতির সঙ্গেই অন্তর্লীন হয়েছিলেন। বৃক্ষের বিনাশ দেখে কবির হৃদয় হাহাকার করে উঠেছিল। বৃক্ষের বিনাশ হলে মানুষের ধ্বংস অনিবার্য। জীবনানন্দ দাশ বলেছেন
‘বড় বড় গাছ কেটে ফেলছে তারা।
এইসব উঁচু উঁচু গাছকে আমার ইচ্ছা লালন করেছিল;
আমার দেহের ভেতর রক্তাক্ত কাঠের গন্ধ;
আমার মনের শহরও সভ্যতার মতো শূন্যতা;
আমি দিনের আলোয়
কিংবা নক্ষত্র যে আভা আনে রাতের পরে রাতে
এই মৃত গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি।’
তিরিশের সর্বাধিক নাগরিক কবি বলে পরিচিত অমিয় চক্রবর্তী গাছ নিয়ে একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। নগর জীবনের সংকট মুক্তির জন্য তিনি বৃক্ষের সাধনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিরিশের পরবর্তী কবিরাও একই ভাবে বৃক্ষ বন্দনা করেছেন।
কবিরা বৃক্ষ নিয়ে প্রেমের চেয়ে কিছু কম কবিতা লেখেননি। কিন্তু বৃক্ষ নিয়ে আজকের উপলব্ধি আলাদা। আজকে প্রাণের তাগিদে, মানব সভ্যতার প্রয়োজনে বৃক্ষের পক্ষে অবস্থান নিতে হচ্ছে। বৃক্ষের পক্ষে না দাঁড়ালে খুব শিগগির মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।
মানুষ অবিবেচকের মতো বৃক্ষ নিধন করে যাচ্ছে। আজকের লোভ এবং যান্ত্রিক প্রয়োজন মেটানোই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এতে ভবিষ্যতের পৃথিবী এবং ভবিষ্যতের মানুষ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে।
মানুষ অবিবেচকের মতো বৃক্ষ নিধন করে যাচ্ছে। আজকের লোভ এবং যান্ত্রিক প্রয়োজন মেটানোই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এতে ভবিষ্যতের পৃথিবী এবং ভবিষ্যতের মানুষ হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। বৃক্ষের পক্ষে আজ বিশ্বব্যাপী আন্দোলন আরও জোরদার হওয়া প্রয়োজন। বৃক্ষ নিধনের ক্ষেত্রে যদিও আমাদের মতো শিল্প-অনুন্নত দেশের চেয়ে শিল্প-উন্নত দেশই তাদের চাহিদা মেটাতে জল্লাদের ভূমিকা নিয়েছে, তবু বৃক্ষের অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে সবচেয়ে আগে আমাদের মতো অনুন্নত দেশ। প্রতি বছর পৃথিবী থেকে এক কোটি সত্তর লক্ষ হেক্টর জমির বৃক্ষ নিধন হচ্ছে। শুধু মাত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার রবিবার সংস্করণ প্রকাশ করতে ২৫ হেক্টর জমির বৃক্ষ নিধন করতে হয়। ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অরণ্য নিধনের পরিমান ১.২ শতাংশ।
আজ থেকে একশ’ বছর আগে বাংলাদেশে বৃক্ষের পরিমাণ ছিল এখনকার চেয়ে তিনগুন বেশি। যদিও দৃশ্যত সামাজিক বনায়ন বেড়েছে, অরণ্য নিধন হয়েছে। একটি দেশের প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যে ন্যূনতম অরণ্যের প্রয়োজন আমাদের দেশে রয়েছে তার কয়েকগুণ কম। পৃথিবীর ৯৫ শতাংশ শুষ্ক ও উষর জমি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। বৃক্ষ অপসারণ ও জমি অপব্যবহারের ফলে পৃথিবীর উপরের যে মাটির স্তর আছে তা অবিশ্বাস্যহারে লুপ্ত হচ্ছে। এই মাটির স্তর তৈরি করতে পৃথিবীর লেগেছিল হাজার হাজার বছর, কিন্তু অরণ্য ধ্বংস হলে তা কয়েক বছরের মধ্যে ধুয়ে নেবে নদী, সমুদ্র। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে, নদীর গভীরতা কমে যাবে। দেখা দেবে ভয়াবহ বন্যা। এই ভাবে বৃক্ষ নিধন চলতে থাকলে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের পানি স্থলভাগ দখল করে নেবে। এভাবে চলতে থাকলে খুব শিগগির স্থলভাগের ৩০ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।
৩.
সভ্যতার অর্থ হলো কৃত্রিম। প্রকৃতি হলো অকৃত্রিম। সভ্যতার প্রবর্তন ঘটিয়েছে মানুষ। আর কোনো প্রাণী এই ক্ষমতা অর্জন করেনি। তাই মানুষ হলো প্রকৃতি বিরোধী। আমরা যে অরণ্য, মহাসমুদ্র, নদ-নদী, পর্বত, মলয়-সমীর কিংবা পৃথিবীর বাইরের গ্রহ-নক্ষত্ররাজির বিন্যাসে মুগ্ধ ও বিষ্মিত হই তার কোনোটাই সৃষ্টি করেনি মানুষ। মানুষ মাটি পুড়িয়ে ভবন নির্মাণ করেছে। অথচ কয়েক দশক আগেও আমরা লক্ষ করেছি ইটভাটাগুলোতে প্রথম অগ্নি সংযোগের লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। কারণ মাটি তো মা; যে মা মায়েরও মা, যে মা আমাদের জীবন দান ও জীবন ধারণ করে রেখেছে তাকে কি কেউ দগ্ধ করতে পারে। এখন আর কেউ সে কথা ভাবে না। মাটি যে আমাদের মা সে কথা আজ আমরা ভুলে গেছি। আমাদের অনুভূতিতে আর তার স্থান নেই। তার শরীর নিবর্তন করে কেবল সুখ খোঁজা। অথচ আগে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে একটি সমবায়ী সহাবস্থান গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ক্ষুধা অনেক বেশি। সে কেবল মাটির উপরে নিবর্তন করছে না। জলেস্থলে পর্বতে তুলছে তুমুল স্বেচ্ছাচারী আচরণ। মাটির তল থেকে বের করে আনছে তরল সোনা। বসুমাতাকে নিরাভরণ না করে তার মুক্তি নেই।
আর এসবই মানুষ করছে তার অতিরিক্ত লোভের বশবর্তী হয়ে। এই পৃথিবীর সম্পদের কোনো রিক্ততা নেই। মানুষ যদি সাম্য বন্টনের মাধ্যমে তার প্রয়োজন অনুসারে তা ব্যবহার করতেন তাহলে হয়তো তার বিলয় ছিল না। কিন্তু অস্বাভাবিকতা পৃথিবী সহ্য করে না। প্রকৃতি নিজেই তার চিকিৎসক। এভাবে চলতে থাকলে একদিন সে সব কিছু নতুন করে শুরু করবে। বিলুপ্ত হবে সভ্যের বর্বর লোভ। বর্তমান মহামারি কি তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে!