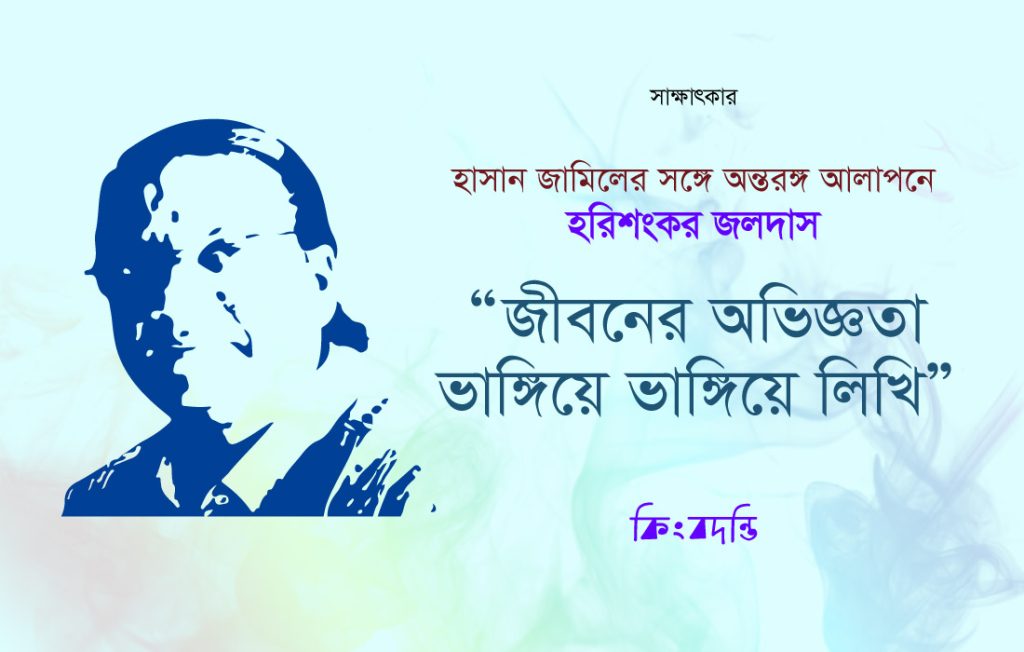হরিশংকর জলদাস বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যের মূল ফোকাসের জায়গাটা নিন্মবর্গ। জেলে জীবন দেখেছেন নিজের যাপনের ভেতর দিয়েই। শিক্ষকতা করতেন। বাংলার অধ্যাপক ছিলেন, ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল। পৌরাণিক কাহিনীর সাথে বর্তমানের সেতু রচনা, নিন্মবর্গের জীবনের সাথে মেইনস্ট্রিমের- এইটাই তাঁর সাধনার জায়গা। উপন্যাস লিখেছেন একলব্য বা শকুনির মতো পৌরাণিক চরিত্র নিয়ে, লিখেছেন নিজের দেখা জেলে জীবন, হরিজন ও দেহজীবীদের নিয়ে। তিনি নিজেই বলেন, অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি লিখেন না, লিখতে চান না। বিচিত্র বৈভবে সাজানো তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তিনি আন্তরিক আলাপ করেছেন তাঁর বেড়ে উঠা, স্ট্রাগল, সাহিত্যিক জার্নি ও পরিকল্পনা নিয়ে। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি ২০১৯ সালের বইমেলার সময় নেয়া হয়েছিল। প্রকাশ হয়েছিল চ্যানেল আই অনলাইনে। সেসময়ের কিছু সমসাময়িক বিষয় এখন কম প্রাসঙ্গিক, সেসব অংশ কিছুটা কমিয়ে ‘কিংবন্তিতে’ সাক্ষাৎকারটি পুনঃমুদ্রণ করা হলো, এতে সাক্ষাৎকারটির দৈর্ঘ্য কমলো এবং একই সাথে প্রাসঙ্গিকতা বাড়লো বলেই আমরা মনে করি। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন হাসান জামিল।
হাসান জামিলঃ আপনার লেখালেখিতে আসাটা বেশ আগ্রহোদ্দীপক। আপনার লড়াই। আমরা কম বেশি জানি, আপনি অনেকবার বলেছেন। তবু আপনার লেখালেখিতে আসার প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করা যাক…
হরিশংকর জলদাসঃ আসলে লেখালেখি তো করিনি, পড়াশোনা করেছি। আপনি জানেন যে আমাদের, বিশেষ করে আমার ব্যক্তি জীবনটাই মাটিতে বুক ঘষে ঘষে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জীবন। অন্যরা তো দুই পায়ে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছায় কিন্তু সামাজিক অবস্থানের কারণে বা দারিদ্র্যের কারণে, শিক্ষাহীনতার কারণে আমি যেখানে জন্মেছি সেখানে সব সময় শুধু মানুষকে অন্ন চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে হয়। দু’বেলা খেতে পারলেই যেন জীবনটা বেঁচে যায়। কোন রকম খেয়ে-দেয়ে জীবনটাকে আরেকটা জীবনের দিকে বা আর একটা জীবন উৎপাদনের দিকে বা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই একরকমের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল সেইসময়। আমার সময়েও, এখনও। কিন্তু আমি নিজেও যে খুব উৎসাহী হয়ে পড়াশোনা করেছি এমন না। আমার দাদী ছিলেন পরাণেশ্বরী জলদাসী। তাঁরই উদ্দীপনায় আমি লেখাপড়ায়। তিনি নিজেও লেখাপড়া জানতেন না । পরাণেশ্বরী জলদাসীর স্বামী ২১ বছর বয়সে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি, মারা গেছেন। তিনি বিধবা হয়েছেন তিনি ১৭ বছর বয়সে। ছেলে ছিল আড়াই বছর বয়সের। বিচিত্র ক্ষয়াটে, রক্ত ক্ষরিত একটা জীবন ছিল তার।
আমাদের সমাজে সেই সময়ে বিধবা বিবাহের একটা প্রচলন ছিল। যাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ‘সাঙ্গা’ বলে। আমার দিদিমা সেদিকে যাননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর স্বামী যে সন্তান রেখেছেন তাকেই বড় করে তুলবেন। যা হোক, এভাবে জীবন শুরু হয়েছে এবং আমার পড়াশোনার জন্য আমার দাদিমাই সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি একদমই পড়াশোনা জানতেন না। স্বামী মরে যাবার পরে গোটাটা জীবন মাথায় মাছের খারাং নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করেছেন। আমার পড়ালেখার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমি গভীর রাতে কোন টিচারের কাছে প্রাইভেট পড়তে গেলে তিনি গিয়ে নিয়ে আসছেন, কিংবা অপেক্ষা করেছেন আমাকে আনবার জন্য, গ্রামের সেই অন্ধকার রাস্তার ভূতুরে পরিবেশ অতিক্রম করে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতেন। তার অনুপ্রেরণাতেই আমার পড়াশোনা বাঁচিয়ে রাখা। বাবা তো ছিলেনই। বাবা তখন বলেছিলেন ‘আমার জীবনটাও সমুদ্রে শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার আমার বাবাও মরেছেন, তোদের আমি সমুদ্রে মরতে দিতে চাই না’। সেটা থেকেও পড়ার প্রতি একধরণের আগ্রহ আমার জন্মেছে। সেটাকে একেবারেই বৈষয়িক লেখাপড়া বলা যায়।
সেই সময় থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতাম যদি আমি এসএসসি পাশ করতে পারি তাহলে একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হবো। এবং শিক্ষক হলেই কিছু বেতন পাবো। ঐ বেতন পেলেই আমার পরিবারের অন্নসংস্থান হবে, স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। এইটুকু ভেবে ভেবেই আমার পড়াশোনা করা। এসএসসি পাশ করার পর আমার ভেতরে জাগলো যে না এইচএসসি পাশ করতে হবে। এইচএসসি পাশ করবার পরে আরও অনার্স টনার্স পড়তে যাওয়া। আপনি বলছিলেন যে লেখালেখির ব্যাপারটা, লেখালেখির ব্যাপারে একধরণের প্রস্তুতি থাকে আপনি যাকেই জিজ্ঞেস করুন। কিন্তু লেখালেখি করবার জন্য আমার কোন প্রস্তুতি ছিল না। স্বপ্নেও আমি ভাবিনি যে লিখব। তবে হ্যাঁ, আমি পড়াশোনা করতাম। আমাদের বাড়ির মধ্যে একটা ছোট্ট মাটির ঘর ছিল। যাকে আমার দাদীমা’রা মন্দির হিসেবে ব্যবহার করত। বাবা সেখানে দুটো বই রেখেছেন। বাবা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছেন। একটা কাশীরাম দাসের মহাভারত। আরেকটা হলো রামায়ণ। এগুলো উনারা রাখতেন আসলে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে। কিন্তু আমার কাছে সেগুলো কখনও ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। আমি সেখানে গল্পের রস সংগ্রহ করতাম।
বাবা একদিন বললেন, তখন আমি থ্রি বা ফোরে পড়ি, তুই তো পড়তে শিখছিস- দেখ এইগুলো পড়তে পারিস কি না! তো পড়তে পড়তে, গল্পের প্রতি, কাহিনীর প্রতি আমার যে তৃষ্ণা ছিল সেটা জেগে উঠে। তখন আর বয়স কত, ১০-১২ বছর, তখনই গদ্যের প্রতি প্রলুব্ধ হয়েছি। ভালো রকমেই প্রলুব্ধ হয়েছি। যখন যা পেয়েছি গল্প বা উপন্যাসের আকারে তা পড়ে পড়ে গেছি। আর লেখালেখির ব্যাপারটা বলছেন? লেখালেখি যারা করতেন তাদের দিকে আমি দূর থেকে বিচিত্র চোখে, শ্রদ্ধার চোখে তাকাতাম। আহা, তারা কি রকম যেন অন্য জগতের মানুষ! স্বর্গীয় মানুষ। তাদের হাত দিয়েই তো মানুষের জীবনের চালচিত্রগুলো তৈরি হয়। কি অসাধারণ মানুষ হতে পারেন! তাদের কাছে কখনও যাইনি। আপনি জানেন, হয়তো গ্রন্থান্তরে পড়েছেন, আমি সরকারি চাকরিতে এসছি, পড়াতে পড়াতে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়েছি, নিন্দার শিকার হয়েছি, অবহেলার শিকার হয়েছি। এই অবহেলাজনিত প্রচণ্ড একটা আঘাতের শিকার হয়েই আসলে আমি লেখালেখি করছি।
আপনি ধরুন একজন হিন্দুর ছেলেকে হিন্দুর ছেলে বললে অপমানের কিছু নেই, একজন মুসলমানের ছেলেকে মুসলমানের ছেলে বললে অপমানের কিছু নেই, এমন কি একজন জেলের ছেলেকে জেলের ছেলে বললেও অপমানের তেমন কিছু নেই কিন্তু সেই শব্দটা যখন ‘জাইল্যার পোলা’ হয়ে যায় সেখানে একধরণের বিকৃতি আসে। আপনি ধরেন যদুমোহন। এই যদুমোহন তুই কোথায় যাস?- এইটা বললে কিছু মনে করবে না। কিন্তু আমরা যখন তাকে বিকৃত করে বলি, ‘এই যউদ্দা কোথায় যাস?’ তখন সে যতই অশিক্ষিত হোক, যতই মাটির সাথে বুক ঘষে ঘষে চলার মানুষ হোক, সে কিন্তু অবশ্যই ব্যথা পাবে। তো আমাকে সেই ‘জাইল্যার পোলা’ বলে সম্বোধন করতেন যখন আমি বিসিএস টিসিএস দিয়ে এসিস্টেন্ট প্রফেসর হয়ে গেছি প্রায়, সরকারি কলেজে। এই নিন্দার, অবহেলার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার আসলে পড়াশোনা আরও গভীরভাবে শুরু করা। বিশেষ একটা বিষয়কে নিয়ে পড়াশোনা শুরু করা।
জেলেরা নিন্দিত কি না, এরা অবহেলিত কি না- তাতেই হঠাৎ একদিন আমার লেখার প্রতি আগ্রহ হলো। আমার প্রথম যখন উপন্যাস বের হয়, আমার বয়স ৫৫ বছর। ভেবে দেখুন একটু। মুসলিম বা হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মের যারা আছেন বা অন্যান্য ধর্মেরও, তারা তখন ধর্মানুরক্ত হয়ে পড়েন , জীবনের বেশির ভাগ পথ অতিক্রম করবার পর মানুষের মধ্যে ধর্মানুভুতি বলেন বা ধর্ম ভীতিই বলেন- চলে আসে, এগুলো জাগে ; তো আমারও জাগা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু ঐ সময়ই আমাকে আমার অস্তিত্ত্ব্বের সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই কলম ধরতে হয়েছে। এবং তখনই আমার ‘জলপুত্র’ উপন্যাসটি লেখা। লিখবার জন্য আমার কোন প্রস্তুতি ছিল না, ছিলই না। কখনও আমি চিন্তাই করিনি। এটা একটা এক্সিডেন্টাল ব্যাপার। এবং প্রস্তুতি ছাড়া যদি কেউ লিখা লিখে থাকেন তাহলে সেটা হয়তোবা আমি! অধিক বয়সে অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু তাদের হয়তো প্রস্তুতি ছিল। আমি একদম প্রস্তুতিহীন ভাবেই… ঐ যে বলে না, চড় খেয়ে পেছন ফিরে তাকানো, আমিও ঐ সামাজিক বৈষম্যের চড় খেয়ে লেখালেখি শুরু করেছি।
হাসান জামিলঃ আপনি এখনই মহাভারতের কথা বলতেছিলেন, বলতেছিলেন আপনার জেলে পরিবার থেকে উঠে আসার কথা। আপনার লেখাতেও দেখা যায়, লেখার মূল ফোকাস পৌরাণিক কাহিনী বা নিন্মবর্গ। বাংলাদেশের মত দেশে, মধ্যবিত্ত যেখানে বইয়ের ভোক্তা, সেখানে তাদের দিকে তাকালেন না কেন?
হরিশংকর জলদাসঃ জেলেদের মধ্যবিত্ত বলবেন না আমি নিশ্চিত জানি, আমি হরিজনদের নিয়ে লিখেছি তারা মধ্যবিত্ত না, আমি দেহজীবীনীদের নিয়ে লিখেছি তারাও মধ্যবিত্ত না। এইটার একটা সোজাসাপ্টা উত্তর হতে পারে, মধ্যবিত্ত জীবন ব্যবস্থা কি আমি সম্ভবত চিনি না। অথবা এইটা বলতে পারি, আমার গোটা জীবনের যে অভিজ্ঞতা তা ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে লিখি; কোন আরোপিত, কোন ধার করা অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখি না। নিন্মবিত্ত সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছি বলেই ঐ সমাজটাকে আমার ভালো করে চেনা আছে। সে জন্য তাদেরকে নিয়ে লিখি। তবে, এই কথা এখানে একেবারেই বলা যাবে না যে, আমি মধ্যবিত্তদের নিয়ে লিখি না। আমার ‘হৃদয়নদী’ নামে একটা উপন্যাস আছে, ‘এখন তুমি কেমন আছো’ নামে একটা উপন্যাস আছে। এই দুটো উপন্যাসে আমি মধ্যবিত্ত জীবন ব্যবস্থাকে নিয়ে লিখেছি। তবে প্রত্যেক লেখকের কিন্তু একটা গন্তব্য থাকে।
যারাই লিখছেন, তাদের কারও কারও বলার বিষয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি, কারও কারও বলার বিষয় উচ্চবিত্ত শ্রেণি, কারও বলার বিষয় পৌরাণিক কাহিনী, কারও বলার বিষয় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো- সেটা গল্পের ছলে হোক কিংবা প্রবন্ধের ছলে বা কবিতার ছলে। আমি প্রথমত ঐ জীবনটাকে, ঐ সমাজটাকে ভালো করে চিনি বলেই তাদের নিয়ে লেখি। পৌরাণিকের যে ব্যাপারটা বলেছেন, আমি একলব্যকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছি আর শকুনিকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছি। আমরা যে বলি শকুনি মামা। নিন্দা করি আমরা। তাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছি, নাম দিয়েছি ‘সেই আমি নই আমি’। ইদানিং ‘কালের কণ্ঠ’তে আমার একটা ধারাবাহিক উপন্যাস যাচ্ছে, ‘মৎস্যগন্ধা’ নামে। যেটা বললাম, ছোটবেলায় মহাভারত দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলাম, আপ্লুত হয়েছিলাম।
মহাভারত আমাকে দখল করে নিয়েছিল। আপনি যদি দৃষ্টিকে একটু ক্ষীণ করে, তিব্র করে তাকান আমার লেখার দিকে, আপনি দেখবেন আমি যাদের নিয়ে লিখেছি, তারাও কিন্তু সমাজের নিন্মবর্গের মানুষ। একলব্য ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের কাছে বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, ঘৃণায় তাকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। একলব্য নিজে চেষ্টা করে অরণ্যের মধ্যে অস্ত্র শিক্ষা করেছেন। যখন তিনি অসাধারণভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন তখন দ্রোণাচার্যর মধ্যে ব্রাহ্মণ্য চিন্তা জাগলো। তাকে তো দাঁড়াতে দেয়া যাবে না। ও তো নমঃশূদ্র। আর্য সমাজ ব্যবস্থার বাইরের। সে যদি বড় হয়ে উঠে তাহলে আর্য সমাজ ব্যবস্থাকে সে ধ্বংস করতে উদ্ধত হবে। ফলে কৌশলে গুরুর ভান নিয়ে, শিক্ষকের দোহায় দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা গুরুদক্ষিণা হিসেবে কেটে নিয়েছিল।
তীর চালাবার জন্য অথবা তরবারি চালাবার জন্য ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল অপরিহার্য। সেই অপরিহার্য আঙুলটাই তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন। এইটা কি যারা নিন্মবর্ণের-নিন্মবর্গের তাদের ধ্বংস করবার একটা পাঁয়তারা নয়! শিক্ষক না হয়েও তিনি শিক্ষকের দাবীতে গুরুদক্ষিণা নিলেন। শকুনির কথা যা বলছিলাম, শকুনি আমাদের সমাজের মধ্যে, সে একেবারে আর্য সমাজ থেকে শুরু করে নিন্দার্থক বাগধারাই অংশ হয়ে গেছে। আমাদের এখানে ‘শকুনি মামা’ মানে এমন এক আত্মীয় যে আত্মীয় ক্ষতি করে। কিন্তু মামা আসলে ক্ষতি করছে কেন? আমাদের সমাজে একটা কথা আছে না, যার মামা এবং শ্বশুর নাই তার উন্নতি নাই। কিন্তু এই মামা একেবারেই আপন মামা হয়ে কেন ভাগনেদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলেন? তার পশ্চাতে একটা কারণ আছে। দুর্যোধনরা মিলে শকুনির বাবা মা’কে হত্যা করেছে, ৯৯ জন ভাইকে হত্যা করেছে তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য আত্মীয়ের বিপক্ষে গেছেন কিন্তু তার ভেতরে একধরণের রক্ত মাংসের ভালোবাসা ছিল, ঈর্ষাবৃত্তি ছিল, ক্রুরতা ছিল, তিনিও বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। আমি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেছি যে শকুনির ভেতরে কি মানবতাবোধ ছিল না! সে দৃষ্টি থেকেই উপন্যাসটি আমি লেখার চেষ্টা করেছি।
রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনীকে নিয়ে লিখেছি, ‘আমি মৃণালিনী নই’। অনেকেই এই উপন্যাসটা নিয়ে জানতে চেয়েছেন। আমি কি উপন্যাসটিতে রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করেছি? আসলে আমি কোন কটাক্ষ করিনি। তাঁর জীবনের মধ্যে যে উপাদানগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সে বিষয়গুলো আমি উপস্থাপন করেছি শুধু। রবীন্দ্রনাথ তার স্ত্রীর প্রতি আমার বিবেচনায় অবহেলা দেখিয়েছেন। অন্যান্যদের প্রতি তিনি যতটা সচেতন ছিলেন, স্ত্রীর প্রতি ততটা ছিলেন না। তাঁর নাম ছিল ভবতারিণী দেবী। ঠাকুর বাড়িতে তাঁর নাম হয় মৃণালিনী দেবী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিন, না চিঠিতে না কথায়, মৃণালিনীকে মৃণালিনী ডাকেননি। নামটা কেড়ে নিলেন, তাঁকে তাঁর বাবা মা যে নামটা দিয়েছিলেন, তা কেড়ে নিলেন, কিন্তু সেই নামের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ কোন দিন দিলেন না। এই যে বিষয়গুলো, যেন একধরণের সর্বহারা, একধরণের প্রান্ত মানুষদের জীবন কাহিনী নয় কি? রবীন্দ্রনাথের কাছেও কি মৃণালিনী প্রান্ত মানুষ রয়ে যান নাই? এখানে রবীন্দ্রনাথ সাপেক্ষে মৃণালিনী নিন্মবর্গ। নিন্মবর্গ বলতেই খালি জেলে মেথর মুচি ইত্যাদি বুঝলে চলবে না।
হাসান জামিলঃ আপনার উপন্যাসে আমরা একটা বর্ণ সমন্বয় বা ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা দেখি। আমি এই প্রসঙ্গে রামগোলামের কথা বলতে পারি। ‘রাম’ ও ‘গোলাম’ শব্দ দুইটা দুইটা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে, আপনি উপন্যাসেও চরিত্রের মুখ দিয়ে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেন সচেতন ভাবে আপনি সেইটা করেন…
হরিশংকর জলদাসঃ আসলে আমি বলি, ধর্মগতভাবে তো আমাদের ছোটবেলা থেকেই দূরে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে নিন্মবর্ণ বলে। হিন্দু পাড়ায় আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করা হতো। কিন্তু ওদেরকে খেতে দিতো, যারা হিন্দু- টেবিলে; আমাদেরকে খেতে দিতো উঠোনের এককোণে বাঁশ পেতে বাঁশের সামনে কলাপাতা দিয়ে মাটিতে। বলা হতো যে, খাবার পর তোমরা তোমাদের এঁটোগুলো তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের পাশাপাশি দেখছি টেবিলে বসে অন্যান্য হিন্দুরা খাচ্ছে। তো এই রকম অবস্থাতেই আমাদের জীবন শুরু হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভেতরে একধরণের ক্রোধ জাগিয়ে রেখেছে এরা। মেথরদেরও একই অবস্থা। আপনি এখনও দেখেন, কাউকে যদি আমরা মেথর হিসেবে মানে হরিজন হিসেবে চিনে নেই, তাহলে কিন্তু আমরা ওর থেকে দূরে সরে আসি।
আমাদের শহরের মধ্যে, চিটাগাং শহরের মধ্যে, আমরা দেখি, চা দোকানে বসতে দেয়া হয় না তাদেরকে। তাদের চা দিলে জগ দিয়ে দেয়া হয়, তাদেরই একটা নিজস্ব জগ থাকে। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে খায়। যেটা আমি রামগোলামের মধ্যে করেছি। এই বেদনাগুলো আমাকে তাড়িয়েছে। আমি ভেবেছি যে এদের যদি আমরা মেনে না নেই তাহলে কি হবে! এখন তো আমাদের স্যানিটারি পায়খানা হয়েছে । আমাদের জীবনে এদের কত অবদান, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জায়গা থেকে এখনও অপরিহার্য। এদের যদি বুকে টেনে নাও নিতে পারি, অন্তত পাশাপাশি দাঁড়াতে দেয়ার অধিকার দেয়া তো উচিত।
আমি যখন উপন্যাসটার পরিকল্পনা করছি, আমি বলে নেই, চট্টগ্রাম শহরে ৫ টা হরিজন পাড়া আছে, আমি খুব ছোটবেলা থেকে সেখানে যাতায়াত ছিল। কেন ছিল সেটার ব্যাখ্যা আমি ঠিক জানি না, কাকতালীয়ভাবে যাতায়াত ছিল । তাদের আশপাশে আমি ঘুরেছি, তাদেরকে খুব কাছ থেকে আমি দেখেছি। পরবর্তীকালে লিখবার সময় তো আরও বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে। এদের মধ্যে আমি হীনম্মন্যতাবোধটা দেখেছি। এবং এখনও। আমার বাবা ছিলেন একজন সাধারণ জেলে। জেলেদের তো কোন বর্ণগত ঐতিহ্য নেই। তো বাবাও যখন শহরে আসতেন আমাকে নিয়ে, ঐ মেথররা তখন গুয়ের টিন, পাতি টিন নিয়ে যেতেন রাস্তার একপাশ দিয়ে ময়লাগুলো ফেলবার জন্য। বাবা ওদের দেখেই বলতেন, ‘বাবা, ওদের কাছে যাস না, যাস না ওরা অস্পৃশ্য ওদেরকে ছোঁস না…’। যে বাবা নিজেই একজন প্রান্তিক মানুষ সে বাবাই একজনকে দেখিয়ে বলছে। তাহলে একজন অতি নিন্মবর্ণের মানুষও মেথরকে যেখানে ঘৃণা করছে, সেখানে উচ্চবর্ণের মানুষেরা তো ঘৃণা করবেই, করে আসছে এখনও।
আমি উপন্যাসটা লেখার সময় ভেবেছি, এদের মধ্যে একধরণের সাম্য সমতা না আনলে আমার উপন্যাসের কোন সার্থকতা হবে না। এই জন্যই নাম দিয়েছি রামগোলাম। হিন্দুদের যে দশজন অবতার আছেন, তার মধ্যে রাম একজন। আর গোলাম, আপনারা জানেন যে গোলামে মোস্তফা মানে মোস্তফার সেবক। সেই শব্দটা আসলে ইসলামিজমের সাথে, ইসলামের পবিত্রতার সাথে যুক্ত। আমি ইসলামের সাম্যবাদটা আর হিন্দুদের দেবত্বটাকে সমন্বয় করে এই নামটা দিয়েছি। এবং আমার উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের মধ্যেই চরিত্রের মুখ দিয়ে আমি বলিয়েছি কেন উপন্যাসের নাম রামগোলাম।
হাসান জামিলঃ এই প্রসঙ্গের থাকা যাক আর একটু। বাংলাদেশে জনসংখ্যার দিক দিয়ে কম থাকায় হয়তো কাস্টের ব্যাপারটা অত চোখে পড়ে না। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে তো দীর্ঘ লড়াই। আধুনিক ভারতে আম্বেতকরের কথা আমরা বলতে পারি। এখন গিয়ে দেখা যাচ্ছে ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা ক্ষমতায়। ওখানে কাস্ট প্রসঙ্গটা হালে আরও পানি পাইছে। আমাদের দেশে অবস্থাটা কি?
হরিশংকর জলদাসঃ আম্বেতকর লড়াই করেননি শুধু, শেষ পর্যন্ত তিনি হিন্দু ধর্ম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাঁকে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁদেরকে, তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের কোন জল স্পর্শ পর্যন্ত করতে দেয়া হতো না! জলের অপর নাম প্রাণ, সেই জল পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেয়া হতো না। সেই ক্রুরতা থেকে হোক, অভিমান থেকে হোক, তিনি ধর্ম ত্যাগ করেছেন। আমি তাঁর জীবন খুঁজে দেখেছি। তিনি চেয়েছিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে। পরবর্তীতে তিনি তাঁর আশপাশের মানুষের কথায় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ধর্মীয় সাম্যর জায়গাটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে তা ইসলাম ধর্মেই তরতাজা প্রাণময় একটা অস্তিত্ব পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে বিষয়টা জটিল হয়ে যাবে, জীবনের বিবর্তনটা আরও গাঢ় হয়ে যাবে। কথা ঐটা না, ধর্মান্তরিতের বিষয়টা না। কথা হলো যে এটা একধরণের চড় দেয়ার চেষ্টা করা তাদেরকে, যারা বর্ণবাদের বিষয়টাকে প্রকটভাবে দেখে।
আর বাংলাদেশের কথা যদি বলি তাহলে কয়েক রকম উত্তর পাবেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলে এক রকম পাবেন আর কোন বর্ণহিন্দুকে যারা চৌধুরী, সেনগুপ্ত, চক্রবর্তী, বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের প্রশ্ন করলে এক ধরণের উত্তর পাবেন। তাঁরা বলবেন যে, ‘না না না ওসব এখন আর নাই’! আরেকটা ব্যাপার আছে, ঢাকা বা চট্টগ্রাম শহরের কোন হিন্দুকে জিজ্ঞেস করলে এক ধরণের উত্তর পাবেন, গ্রামের একজনকে জিজ্ঞেস করলে আরেক ধরণের উত্তর পাবেন। শহর কেন্দ্রিক যারা, যারা মেট্রোপলিটন জীবন যাপন করছেন, তাঁরা বলবেন, ‘আরে না, সমজের মধ্যে এখন আর এইগুলা আছে না কি, দেখেন না অমুককে তমুক বিয়ে করেছে তমুককে অমুকে বিয়ে করেছে’! কিন্তু ঢাকা চট্টগ্রাম তো বাংলাদেশ নয়, তার বাইরে গোটা বাংলাদেশ ছড়িয়ে আছে। সেখানে এই বর্ণ ব্যবস্থাটা, হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা অবহেলা এখনও আছে- প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এরা কাগজে বলছে ‘হরিশংকর আমার ভাই, হরিশংকর আমার ভাই… তাঁর মতো মানুষ হয় না কি…’। কিন্তু পেছনে গিয়ে বলছে…
আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই, শেষ জীবনে আমি চট্টগ্রাম সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলাম। আমাদের ওখানে ডিসি হিল বলে একটা জায়গা আছে মর্নিং ওয়াকের। আমি হেঁটে যাচ্ছি, এক ভদ্র লোক, তাঁর সঙ্গে তিন-চার জন বন্ধুবান্ধবও ছিল, আমাকে সামনে সালাম দিলেন, আমি প্রতিউত্তর দিলাম। আমাকে ছাড়িয়ে দু’কদম পেছনে গিয়ে পাশের জনকে বলছেন, ‘হরিশংকর জলদাস, সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল, জেলে কিন্তু’! এখন আপনি বলেন, আহমদ রেজা, সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল মুসলমান কিন্তু বা হরিপদ চক্রবর্তী সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল, হিন্দু কিন্তু- এই কথা তো বলবে না সে, কেউ বলে না। এই কথাটা কি শুধু আমাদের জন্যই তোলা রাখবে মানুষরা! আমি ধরেন অনার্স পাশ করবার পরে, বিসিএস হবার পরে, অনেক বেদনার্ত হয়ে পিএইচডি করার পরে; নাড়ির প্রত্যাঘাতের জন্য আমাকে পিএইচডিও করতে হয়েছে, ‘নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জীবন’ নামে; আমি প্রিন্সিপাল হওয়ার পরেও আমার যখন পরিচয় দেয়া হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে আমি জাইল্যা! আর কত বছর, আর কত কি অর্জন করলে, আর কত পড়াশোনা করলে, বুক ঘষে ঘষে আর কতটুকু গেলে আমাকে জাইল্যা না বলে শুধু বলবে, আমি হরিশংকর জলদাস!
হাসান জামিলঃ আমাদের এখানে, বাংলাদেশ অংশে, ‘নমঃশূদ্র’ নামে পত্রিকা ছিল আপনি জানেন। বরিশালের স্বরুপকাঠি থেকে ‘নমঃশূদ্র দ্বিজতত্ত্ব’ বের হলো। কিন্তু এখন এইখানে এখন আর এই চর্চাটা চোখে পড়ে না। যেটা দেখা যায় পশ্চিম বাংলায়, গোটা ভারতে। অনিল ঘরাই, মহিতোষ বিশ্বাস, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, সমরেন্দ্র বৈদ্য, সুনীল কুমার দাস প্রমুখ যেমন গুছিয়ে দলিত সাহিত্য চর্চা করছেন। আমাদের বাংলাদেশে প্রধানত আপনাকেই দেখা যায়। কেন এইখানে হচ্ছে না বা অবস্থাটা কী?
হরিশংকর জলদাসঃ দলিত শব্দটা নিয়েই আমার আপত্তি আছে। দলিত কথাটা আসলেই আমার মাথার মধ্যে একটা বেদনা জেগে উঠে। একটা উদাহরণ দেই, একটা সিগারেট খেতে খেতে যখন শেষ করলেন তখন আপনি সেটা ফেলে জুতার শুঁকতলি দিয়ে সেটা দলিত করলেন, পিশে দিলেন। কেন? আগুন নিভে যাওয়ার জন্য! আমাদেরকে, যারা প্রান্ত জনগণ, তাদেরকে কেন যে দলিত শব্দটা দিয়ে অভিহিত করা হয় আমি বুঝতে পারি না। এই দলিত শব্দ শুনলেই কিন্তু আমার জুতার শুঁকতলির কথা মনে পড়ে, সিগারেটের শেষ অংশের কথা মনে পড়ে। আমাদেরকে কি জানিয়ে দেয়া হচ্ছে তোমরা যতই সাহিত্য করো না কেন, তোমাদের সাহিত্য কিন্তু দলিত সাহিত্য হিসাবেই পরিচিত হবে! তোমাদের শেষ পরিণতি হবে জুতার শুঁকতলির নিচে। এই দলিত শব্দটা ব্যবহার না করে যদি আমাদের জন্য প্রান্তিক/ অন্ত্যজ/ প্রান্তজন শব্দটা ব্যবহার করে তাহলে আমাদের সম্মানটা থাকে। আমাদের অস্তিত্বটা একটু মুক্তি পায়। দলিত শব্দ দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব লাঞ্ছিত হয় বলে আমি মনে করি।
আপনি প্রশ্ন করেছিলেন দলিত সাহিত্য নিয়ে। কলকাতায় বলেন কি উত্তর প্রদেশেই বলেন বা গুজরাট বলেন ওখানে দলিত সাহিত্যটা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেক খ্যাতিমান রাইটাররা লিখছেন। কবিতা লিখছেন গল্প লিখছেন প্রবন্ধ লিখছেন উপন্যাস লিখছেন। চার দিকে একটা কাঁপানো ভাব আছে। যদি দলগত ভাবে হয় তাহলে এটা সম্ভব। কিন্তু একা একা যদি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বলেন, আমার দাবী মানতে হবে , আমার কথা শুনতে হবে- তাহলে কিন্তু কেউ শুনবে না। যদি ৫০ জন মানুষ একটা মিছিল দেই তাহলে যারা যাচ্ছে তারা কিন্তু শুনতে চাইবে এরা কি বলছে। তেমনি দলগত উচ্চারণটা আসলে জরুরি। একক কণ্ঠস্বর একসময় থেমে যাবে। আমি ঠিক জানি না, বাংলাদেশেও হয়তো প্রান্তজ সাহিত্য নিয়ে কাজ করছেন। সেটাও হয়তো অঞ্চল ভিত্তিক বা দুই চারটা প্রবন্ধ নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করি আমাদের অস্তিত্ত্বে জন্য, অস্তিত্ত্ব না শুধু, আমরা সম্মানটুকু চাই। সেই জায়গা থেকেই লেখা লেখিতে এসবকে প্রাসঙ্গিক করা উচিৎ।
জানেন কি না জানি না, পবিত্র সরকার, পণ্ডিত মানুষ, তিনি কিন্তু জেলে। তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছেন। তিনি বরিশালে জন্মগ্রহন করেছেন। ওদের পদবী ছিল সরকার। এবং তিনি সরকার পদবী অস্বীকার করেন না। আমি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার বক্তৃতা দিতে গিয়েছি, সেখানে তিনিও ছিলেন। আমাকে বলতে দেয়া হয়েছিল , ‘সাহিত্য ও সমাজে অন্ত্যজ মানুষের অবস্থান’ নিয়ে। আমি বৈদিক যুগ থেকে উদাহরণ ধরে ধরে আমার কথা শেষ করলাম। আমার চারপাশে সবাই, উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা যারা আলোচক ছিলেন, কেউ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেউ চট্টোপাধ্যায়, সবাই খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ঐ সময় পবিত্র সরকারও ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, “শংকর, এইগুলো হয়, এইগুলো করে এরা, তুমি কষ্ট পেও না। কারণ তোমার দলে আমিও, আমি পবিত্র সরকার, আমিও জেলে।”
তো যাই হোক, আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম, আমাদের সমাজে মানুষ এই নিন্দার হাত থেকে এই অবহেলার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পদবী চেঞ্জ করছে। কেউ সেন লিখছে, কেউ চৌধুরী লিখছে; নিচের পক্ষে দাশ লিখছে। এইযে পদবী পরিবর্তন করছে, তাতে কাল হচ্ছে। একসময় আর আপনি এদের খুঁজে পাবেন না। ময়ূরপুচ্ছধারী কিছু কাক পাবেন, যারা সব সময় মুখ লুকিয়ে রাখবে সমাজের মধ্যে, যদি ধরা পড়ে! তারা যে জেলে, যদি ধরা পড়ে! এই বিষয়টা থেকে আমাদের মুক্তির দরকার আছে। আমাদের সমাজের মধ্যেও একটু কাজ করার দরকার আছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে এইটুকু বোঝানো দরকার যে চক্রবর্তী যদি একটা জাত হতে পারে, বড়ুয়ারা যদি একটা সম্প্রদায় হতে পারে, সেনরা যদি একটা সম্প্রদায় হতে পারে, জেলেরাও সম্প্রদায়। তোমারা সেখান থেকে লুকাচ্ছ কেন!
আমাদের জেলেদের মধ্যে কিন্তু কোন ঋণ খেলাপি নাই, খবর নিয়ে দেখেন। কোন বড় ডাকাতের নাম নাই জলদাস। আমরা ডাকাত নই, আমরা ঋণ খেলাপি নই, অন্যায়কারী নই। আমরা কেন বিচলিত হবো আমাদের পদবী নিয়ে! বিচলনের একটা মাত্র কারণ, আমরা ভালোবাসা চাই। প্রচুর ভালোবাসা চাই। খোলা একটা বুক চাই। যে বুকের দুয়ার দিয়ে আপনারা আমাদেরকে টেনে নিবেন। সেখানে গিয়ে আমরা শান্তি পাবো। সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিচলিত হবো না। আরও বেশি করে লিখবার একধরণের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনের মধ্যে জাগবে।
হাসান জামিলঃ কাস্টের প্রশ্নে একটা বিষয় নজর করার আছে, ভারতে ধর্মীয় রাজনীতির একটা উত্থান দেখতে পাই, বাংলাদেশেও অনেকটা। সেখানে কাস্টের ব্যাপারটা আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?
হরিশংকর জলদাসঃ ধর্ম হলো একান্তভাবে মানুষের বিশ্বাসের বিষয়। সব ধর্মের মূল কথা হলো প্রার্থনা করা, বন্দনা করা। প্রার্থনা এবং বন্দনা, আপনি যদি অভিধান খোলেন সেখানে এই দুটো শব্দের অর্থ আছে প্রশংসা করা। যিনি প্রত্যেক ধর্মেরই একজন স্রষ্টাকে মেনে নেন যে, একজন স্রষ্টা আছেন। যিনি আমাদের সৃজন করেছেন , তাঁকে যারা বিশ্বাস করেন, তাঁরা তাঁর প্রশংসা করেন। সেই প্রার্থনা করার পদ্ধতি নানা ধর্মে নানা রকম। এইটা একান্তভাবে একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু সেই বিশ্বাসটাকে বাইরে নিয়ে এসে নিজের প্রয়োজনে মানুষ ব্যবহার করবার চেষ্টা করে সেই ব্যবহারটা তো একধরণের মানবতা বিরোধী হয় বলে আমি মনে করি। যেটা খুব আন্তরিক একটা ব্যাপার সেটা যখন হীন রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা হয়, তা মঙ্গলজনক হবার কথা না। এবং যেখানে এই বিষয়গুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, উঠছে সেখানে দেখবেন সমাজ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। সমাজ পিছিয়ে পড়ছে, মানুষ পিছিয়ে পড়ছে, আর্থসামাজিক উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ছে। বিজেপির কথা আপনি নিশ্চয়ই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন, কিছু মানুষকে এরা শুধু মুগ্ধ না শুধু, মোহমুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু মোহ এমন একটা বিষয়, যা একসময় না একসময় কেটে যাবেই যাবে। মোহ তৈরিই হয় কেটে যাওয়ার জন্য। আজকে যারা মোহে মুগ্ধ হয়েছেন, ধর্মীয় উগ্রতার দিকে গেছেন, এক সময় তাঁরা থাকবেন না, তাদের মোহ থাকবে না। সেই মোহ কেটে গেলেই তাদের সামনে পুণ্য মানববোধ ছাড়া কিছু থাকবে না।
হাসান জামিলঃ আপানাকে লেখার প্লট বাছার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম মনে হয়। ঠিক ট্র্যাডিশনাল জায়গা থেকে না দেখে একটু বাইরে থেকে দেখা। শকুনির কথা বলছিলেন, আমি কসবি উপন্যাসের দেবযানীর কথা মনে করতে পারি। দেহজীবী মানবিক চরিত্র। এইভাবে দেখার চোখটা নিয়ে যদি বলেন।
হরিশংকর জলদাসঃ অনেকেই নানা রকম প্ল্যান প্রোগ্রাম করে লিখতে বসেন । এইটার পরিণতি কি হবে, এইটার জন্য কোন কোন চরিত আনবেন, কীভাবে আনবেন এসব বিষয়গুলো… আমি কিন্তু মনে মনে একটা চরিত্রকে ভেবে নেই বা একটা সময়কে বেছে নেই এবং কোন এক সকাল দুপুর বা রাত্রে কলম নিয়ে বসে যাই। আমার প্রতিবন্ধকতা প্রথম লাইন শুরু করা; সবচে বড় প্রতিবন্ধকতা প্রথম স্তবক লেখা। প্রথম লাইনটা লিখতে পারলে এবং প্রথম স্তবকটা লিখতে পারলেই আমার লেখা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কোন কোন চরিত্র আসবে এবং কে আসবে এইটা কাহিনী নিজেই ঠিক করে। রবীন্দ্রনাথ যে জীবন দেবতার কথা বলছেন, জীবন দেবতা ফেবতা কিছু না, উনি দেবতাবাদের দিকে গেছেন; আসলে প্রত্যেক লেখকের মধ্যেই একটা ঘোর তৈয়ার হয়। এই ঘোরটাই তাঁকে ধাবিত করে কোন দিকে নিয়ে যাবে। যেমন ‘মৎস্যগন্ধা’ আমি লিখছি।
আমি শুধু ভেবেছি যে মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে আমি একটা উপন্যাস লিখবো। তাতেই আমি লেখা শুরু করেছি আর অন্যান্য চরিত্ররা আসছে। মৎস্যগন্ধার মধ্যে যে সব চরিত্র পৌরাণিক, এমন না। আপনি একলব্য পড়লে দেখবেন, আপনি শকুনিকে নিয়ে লেখা উপন্যাসে দেখবেন, পুরাণের সাথে সাথে আমাদের বাস্তব জীবনও উঠে আসছে। আমি শুধু পৌরাণিক কাহিনীই সেখানে লিখিনি। আমি পৌরাণিক কাহিনীর সাথে বর্তমানের জীবন ব্যবস্থার একটা ব্রিজ তুলতেও চেষ্টা করেছি, এবং সেটাই আমার প্রধান থিম ছিল। উপন্যাসের পরিণতি কি হবে সেটা আমি ভেবে রাখি না, ভেবে লিখি না। একটা সময় আমার কলম বলে, এখানে থেমে যাও, আমি থামতে চাই। চরিত্রগুলো আসে, আবার যায়, আসে… আপন খেয়ালে আসে যায়, কাহিনীতে যুক্ত করে বা বিযুক্ত করে তার অন্তর্ধান হয়।
হাসান জামিলঃ আপনার ‘কসবি’ বেশ আলোচিত। আমরা বাংলায় নানান আখ্যানে দেহজীবীদের কথা পড়ছি। সাহিত্যে এইটা নতুন না। কিন্তু কসবিতে যেন প্রধান বিষয় এসেছে প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রস্টিটিউশন। এখানে বেশ্যালয়ের পরিবেশ প্রতিবেশ রাজনীতি ইত্যাদি খেলে যায়। তো এই উপন্যাসটা নির্মাণের বিষয়ে জানতে চাই।
হরিশংকর জলদাসঃ আমি ‘জলপুত্র’ আর ‘দহনকাল’ এই দুইটা উপন্যাস লেখার পরে বেশ সমালোচনা হয় যে, আমি অন্য কিছু লিখতে পারবো না। দহনকালে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধটা এসছে, এইখানে উল্লেখের বাহুল্য নাই যে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপন্যাসটা পড়ে বেশ মুগ্ধ হয়েছেন। ২০১৪ সালের সার্ক সম্মেলন উদ্বোধনের সময় তিনি ১৪ মিনিটের বক্তৃতায় প্রায় ৩ মিনিট কথা বলেছেন এই উপন্যাসটা নিয়ে। তখন আমার খুব আনন্দ লেগেছিল। যা হোক, এই দুটো উপন্যাস বের হবার পরেই সবাই, বিশেষ করে চট্টগ্রামের মানুষ বলতে শুরু করল, হরিশংকর জলদাস আর কি লিখবে, ওর অভিজ্ঞতাই তো জল জাল আর তাদের জীবন নিয়ে, ও ঐগুলোই লিখতে পারবে। তখন আমার মধ্যে একধরণের দুঃখ জাগল। যে আমি কি অন্য কিছু লিখতে পারি না! তখন আমার এই তৃতীয় উপন্যাস, কসবি, এইটা লিখতে হাত দেই। আমি এই উপন্যাস বিষয়ে কথা বলবার আগে একজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, তিনি রিজিয়া রহমান। রিজিয়া রহমান আজ থেকে প্রায় ৪৪-৪৫ বছর আগে ‘রক্তের অক্ষর’ নামে ৬৪ পৃষ্ঠার একটা বই লিখেছিলেন। আজ থেকে ৪৪ বছর আগে কোন নারীর বেশ্যা পল্লীতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি হয়তো পত্রপত্রিকা পড়ে, অন্যদের সাথে কথা বলে এই উপন্যাসটি লেখার চেষ্টা করেন। এবং সার্থকও হয়েছেন বলা যায়।
আর আমার উপন্যাসটার ক্ষেত্রে বলতে গেলে, খুব ছোটবেলা থেকেই আমার এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। দেখার অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা। আমি যে দেবযানী চরিত্রটা লিখেছি, এই মেয়েটা আমাদের পাড়া থেকে পালিয়ে আসা একটা মেয়ে। তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে এসেছিল। পালিয়ে আসার ৬-৭ মাস পরে তার সেই তথাকথিত প্রেমিক তাঁকে চট্টগ্রামের সাহেব পাড়া, সেখানে বেচে দেয়। সেখানে তাঁকে আমি দাঁড়িয়ে খদ্দের খুঁজতে দেখেছি। ঐ দেখাটাই আমার ভেতরে এক ধরণের বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। সে আমার পাড়ার মেয়ে, ওকে আমি বড় হতে দেখেছি। সে প্রায় আমার সমবয়সী ছিল, সে এখানে কেন! কসবিতে একটা মোহিনী চরিত্র আছে, সেটাও দেখা চরিত্র। এবং এরপরে দুবার আমি ওখানে গেছি। আপনি হয়তো একটা প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি কি ওখানকার কাস্টমার ছিলেন? না, আমি ওখানকার কাস্টমার ছিলাম না। তবে ছিলাম না, একথা বললেও ভুল হবে। আমার ‘নোনাজলে ডুবসাঁতার’ নামে আমার একটা আত্মজীবনী আছে। সেখানে আমি বলেছি, আমার দুজন বন্ধুর সাথে আমাকেও একবার বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছিল। সেই বন্ধুকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়ার পরে আমাদেরকে তাড়া করেছিল অন্যান্যরা। আমার এক বন্ধু ওখানে আটকে পড়েছিলো, আমরা দুজনে রেহাই পেয়েছি সেই অনৈতিকতা থেকে বলেন বা বিপদ থেকে বলেন । কিন্তু এটা তিল তিল করে সঞ্চিত জীবনের অভিজ্ঞতাই বলা যায়। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যেভাবেই বলেন।
মানুষের সাথে তো কথা বলেছিই। ঐ যে মোহিনীর কথা বললাম, সর্দারনী, সেও আমাদের পাড়ার মহিলা ছিলেন। স্বামীটা অকর্মণ্য ছিল আর কি! ফলে তার দৈহিক চাহিদা মেটাতে পাড়ারই একজনের সাথে যুক্ত হবার ফলে ধরা পড়েছিলো। ধরা পড়ার পরে তাকে ‘ডেন্ডেরি’ করা হয়। অর্থাৎ চুল মুড়িয়ে গলায় জুতার মালা পরিয়ে পাড়া বেড়ানোকে ডেন্ডেরি বলে। ডেন্ডেরি খাওয়ার পরেই সে রাগ করে এই সাহেব পাড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এই বিষয়গুলো বার বার আমাকে আক্রান্ত করেছে, রক্তাক্ত করেছে। এদের তো একটা জীবন থাকতে পারতো। এই যে দেবযানীর কথা আপনি বলছেন, যদিও আমি দেবযানীকে নিয়ে এসছি নরসিংদী থেকে, কিন্তু তার আসল বাড়ি কিন্তু পতেঙ্গাই। এদের একটা সুন্দর জীবন থাকতে পারতো। একটা উঠোন থাকতে পারতো, উঠোনের পাশে দুই চারটা গাছ থাকতে পারতো, সন্তান থাকতে পারতো। স্বামীর জ্বর হলে তার কপালে জলপট্টি দিতে পারতো… সকল ছেড়ে কেন তার দেহকে মূলধন করে সে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে! এই উপন্যাসটা বিপুল একটা অভিজ্ঞতারই ফসল, শুধু এইটা না, ধরুন যত উপন্যাস আমি লিখেছি- আপনাকে বলেছি আমি সব নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে লিখি, অভিজ্ঞতার বাইরে লিখি না, এখন পর্যন্ত লিখি নাই। যেখানে আমার অভিজ্ঞতা শেষ হয়ে যাবে, সেখানে আমি লেখা বন্ধ করে দেব।
বেশ কয়েকটি গল্প উপন্যাস মৎস্যজীবীদের নিয়ে লিখেছি। এইবছর, বঙ্গোপসাগরের তলায় যে মাছ আছে, সে মাছগুলো নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছি, মাছের মুখে কথা বসিয়ে। শুনলে আশ্চর্য হবেন, এদের মধ্যে গোত্র আছে সম্প্রদায় আছে, রাহাজানি আছে , লুণ্ঠন আছে- জায়গা এবং নারী নিয়ে এরাও যুদ্ধ করে! এদের সুখ-অসুখ আছে, ৪৯ প্রকারের ডাক্তার আছে। যাদের গায়ের চামড়ার রং আর্জেন্টিনার ফুটবল দলের জার্সির মতো। এদের নিয়ে আমি ‘সুখলতার ঘর নেই’ নামে একটা উপন্যাস লিখেছি। ওখানে একটা ইলিশ কন্যার সাথে একটা পাঙ্গাস পুরুষের প্রেম দেখনো হয়েছে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। এদের ভেতর দিয়েই আমি মাছেদের সমাজ ব্যবস্থা দেখিয়েছি। এতদিন আমি মৎস্যজীবীদের জীবন নিয়ে লিখেছি, এবার মৎস্য জীবন নিয়ে লিখলাম।
হাসান জামিলঃ আপনার গল্প থেকে থেকে সিনেমা হচ্ছে…
হরিশংকর জলদাসঃ আমার গল্প নিয়ে দুটো নাটক হয়েছে। ‘ডেন্ডেরি’ নামে একটা গল্প নিয়ে একটা নাটক হয়েছে। আশুতোষ সুজন বানিয়েছেন এটা। ‘এখন তুমি কেমন আছো’ থেকে হাসান নামে একজন পরিচালক নাটক করেছেন। এখন একটা উপন্যাস ও একটি গল্প নিয়ে নাটক এবং ধারাবাহিক হবার প্রস্তুতি চলছে। আমার ‘চরণদাসী’ গল্প থেকে আসাদুজ্জামান সবুজ সিনেমা বানাচ্ছেন, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন, শুটিং শুরু হবে। আমার যে জলপুত্র উপন্যাস আছে , ঐ যে হাসানের কথা বলছিলাম, সেটার ৫-৭ টা মঞ্চায়নও হয়েছে ঢাকার শিল্পকলায়, নাটক করেছে।
হাসান জামিলঃ আনন্দ হয় না রিটেন ফর্ম থেকে ভিডিও ফর্মে দেখতে?
হরিশংকর জলদাসঃ হুম, যে চরিত্রগুলো অস্পষ্ট ছিল সেগুলো চোখের সামনে হাসবে খেলবে কাঁদবে… আনন্দ হয়।
হাসান জামিলঃ বাংলা সাহিত্যের নানা অনুসঙ্গ বইয়ের বুদ্ধদেব বসুর ‘রাতভরে বৃষ্টি’ নিয়ে একটা লেখা আছে আপনার। আপনি যৌনতার প্রকাশ নিয়ে কথা বলেছেন, যৌনতা আর অশ্লীলতার একটা পার্থক্য… আপনার লেখাতেও যৌনতার উপস্থিতি বেশ ভালো ভাবেই আছে। আপনার কসবির বাইরেও ‘লুচ্চা’ নামে একটা লেখার কথা মনে করতে পারি… আপনি যৌনতাকে সাহিত্যে কেমন করে দেখেন বা ডিল করেন?
হরিশংকর জলদাসঃ আমি যেখানে জন্মেছি, প্রায় ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ফাঁক ফোঁকর দিয়ে যৌনতার বিষয়গুলো চোখের সামনে সংগঠিত হতে দেখেছি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তো খুব আড়াল বা রাখঢাক বেশি নাই। যে মেয়ে বিয়ের আগ পর্যন্ত ব্লাউজ পরছে; বিয়ের পর যেই তার একটা সন্তান হয়ে গেলো, সে ব্লাউজ ত্যাগ করলো। তার স্তন বলেন বা তার পিঠ বলেন এইগুলো নিয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেলো। একজন ১৭-১৮ বছরের মেয়ে মানুষের সামনেই তার স্তন বের করে শিশুদের খাওয়াচ্ছে। এইসব বিষয়গুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাছাড়া আমি মনে করি যে, কামহীন মানুষের জীবন কখনও হয় না। যারা ঋষি, ঋষিরাও কিন্তু কামান্ধ হয়েছেন।
আপনি মৎস্যগন্ধার কথা বলছেন; পরাশর, খুব বিখ্যাত একজন ঋষি ছিলেন, তিনি মৎস্যগন্ধাকে ধর্ষণ করে ছেড়েছেন নৌকার মধ্যে। আমি মনে করি আমাদের ৬ টা যে রিপু আছে- কাম, ক্রোধ , লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য; কামটাকে কেন প্রথমে রাখা হয়েছে? শাস্ত্রকাররা এই কাম যদি অবহেলার হতো তাহলে পেছনে রাখতেন। কিন্তু তাকে প্রথমেই স্থান দেয়া হয়েছে। কাম থেকেই পৃথিবী ধ্বংস হয়, কাম থেকেই পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠে। একজন প্রেমিক প্রেমিকা যে হাত ধরে হাঁটছেন, ফ্রয়েড যেমন বলেছেন, মা যে তার শিশুকে আদর করছে, সেখানেও যেন কেমন একটু রিরংসাপরায়ণতা আছে। আর আমি এমন মানুষদের নিয়ে লিখি যাদের কাছে কামটা, যৌনতাটা একটা প্রধান বিষয় হয়ে থাকে। আর আমরা যারা মুখোশ পরা ‘ভদ্দরনোক’ আছি, তারাও তো কামান্ধ। সুযোগ পেলেই আমরা হাত বাড়াই নানা জায়গায়, সেটা হয়তো আড়ালে আবডালে থাকে। সেই কামান্ধ নারী পুরুষদেরকে টেনে তুলাও তো একধরণের সাহিত্যিক কাজ। আমি সেটাই করেছি।
হাসান জামিলঃ আপনি দেরিতে লেখতে এসেছেন। নন ফিকশন দিয়ে শুরু। কিন্তু দেরিতে শুরু করেও আপনার পুরস্কার ভাগ্য খারাপ বলা যায় না।
হরিশংকর জলদাসঃ (হাসতে হাসতে) খারাপ না, খারাপ না; উত্তম উত্তম! ২০০৮ সাল থেকে এই যে ২০১৯ সাল, ১১ বছরে পড়ল আমার লেখক জীবন। এর মধ্যেই একুশে পদকসহ ১৫-১৬ টা পুরস্কার। তাও সব এলনা ফেলনা না। আর আপনি তো জানেন, পুরস্কার দেয়ার হাত তো আমার নেই। আমি সেই মফস্বলে থাকা একজন মানুষ। ঠিক মত চিনি জানিও না। যদি যোগাযোগ করে পুরস্কার পাওয়া যায়, আমি জানি না, সেই স্কোপও আমার নাই। বাংলা একাডেমি পুরস্কার, আলাউল সাহিত্য পুরস্কার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ পুরস্কার, প্রথম আলো পুরস্কার, সমকাল পুরস্কার… আপনি দেখবেন যে এই পুরস্কারগুলো বেশ কয়েকটা কিন্তু আমার বিশেষ কোন গ্রন্থকে নিয়ে। তাহলে হয়ত এইটুকু বলতে পারি, সেই গ্রন্থে এমন কিছু আছে যা মানুষকে স্পর্শ করেছে। জীবনের সুখানুভূতি বা দুঃখবোদের এমন কোন প্রতিফলন আছে যেগুলো যারা বিচারক তাদের হয়তো আকুল করেছে, আপ্লুত করেছে। পুরস্কারটা আসলে তো ভালোবাসারই প্রতিফলন।
হাসান জামিলঃ শেষ প্রশ্ন করি। আপনার পরিকল্পনা কি ভবিষ্যতে? কি করতে চান, কি লিখতে চান যত দিন আছেন?
হরিশংকর জলদাসঃ আমি আসলে অত পরিকল্পনা করে চলি না। আমি প্রথম যখন লিখতে শুরু করি, ভেবেছিলাম পাঁচটা উপন্যাস লিখব, পাঁচটার পর আর লিখবো না। কিন্তু আমি ১৬ টা লিখে ফেলেছি এরই মধ্যে।
ব্রজেন দাস, যিনি ইংলিশ চ্যানেল পারি দিয়েছিলেন, তাঁকে নিয়ে আমার একটা উপন্যাস লেখার ভীষণ আকুতি আছে। আমি বহুদিন পরে জানলাম, তিনি একজন জেলে ছিলেন। আমি জানতাম না। কৃত্তিবাস, যিনি মহাভারত অনুবাদ করেছেন বাংলায়। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর লেখা পড়েছে। অথচ তিনি আমাদের কাছে একেবারেই অপরিজ্ঞাত। তাঁকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আছে। আর গল্প টল্প তো লিখতেই হবে, নানা সময়ে।
ইদানিং আরেকটা কাজ খুব বেড়ে গেছে সেটা হলো ‘বক্তিমা’ দিয়ে বেড়ানো নানা জায়গায়। অনেকেই উৎসাহ পান। আমি ভীষণ অনুৎসাহ বোধ করি। এতে আমার অনেক সময় চলে যায়। লেখার উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়।
অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।
আপনাকেও ধন্যবাদ।